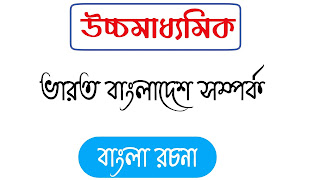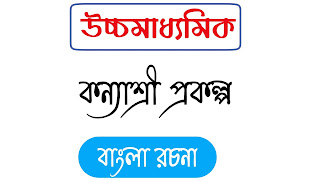ভূমিকা: পানির অপর নাম জীবন। মানুষের জীবন রক্ষাকারী পানি আজ বিষাক্ত হয়ে পড়ছে আর্সেনিকের কারণে। আর্সেনিকযুক্ত পানি জনস্বাস্থ্যের জন্য মারত্মক হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করে মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। ৩০ বছর আগেও দেশের অগভীর নলকূপের পানি বিশুদ্ধ ছিল, কিন্তু ক্রমেই তা আর্সেনিক দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে আর্সেনিক বিষক্রিয়ার কোনো চিকিৎসা নেই।
আর্সেনিকের পরিচিতি: আর্সেনিক একটি বিষাক্ত খনিজ মৌলিক পদার্থ। এর কোনো স্বাদ বা গন্ধ নেই। আর্সেনিকের রাসায়নিক সংকেত A_{s} । পারমাণবিক সংখ্যা ৩৩ এবং পারমাণবিক ভর ৭৪.৯। অর্ধপরিবাহী ও শংকর ধাতু তৈরিতে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। এটি মৌলিক পদার্থ হিসেবে থাকলে পানিতে দ্রবীভূত হয় না এবং বিষাক্তও হয় না। কিন্তু বাতাসে জারিত হয়ে অক্সাইড গঠন করলে এটি বিষাক্ত হয়ে ওঠে।
আর্সেনিকের উৎস: মানুষের দেহে, মৃত্তিকায় এবং সমুদ্রের পানিতে সামান্য পরিমাণ আর্সেনিক লক্ষ্য করা যায়। মাটির উপরিভাগের চেয়ে অভ্যন্তরে আর্সেনিক বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। মাটির নীচে পাথরের একটি স্তর আছে যাতে পাইরাইট্স্ (Fes_{2}) নামে একটি যৌগ আছে। এই যৌগে আর্সেনিক বিদ্যমান। তবে সবচেয়ে বেশি আর্সেনিক দেখা যায় শিলাখন্ডের ভূ-ত্বকে। আর্সেনিক সালফাইড, অক্সাইড ও আর্সেনাইড আর্সেনিকের প্রধান উৎস বলে বিবেচিত। আমাদের দেশে আর্সেনিকের মূল উৎস হলো নলকূপের পানি।
আর্সেনিক দূষণ: দেশে বর্তমানে আর্সেনিক দূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মাটির নীচে বিশেষ স্তরে আর্সেনিক সঞ্চিত থাকে এবং নলকূপের পানির মাধ্যমে তা উত্তোলিত হয়। বিগত কয়েক দশক যাবত কৃষি উৎপাদনে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে ফলে তা বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে দূষিত করছে নদী, নালা, খাল, বিল এবং সমুদ্রের পানি। এই অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার আর্সেনিক দূষণের একটি অন্যতম কারণ। মাটির বিশেষ যে স্তরে আর্সনোপাইরাইট নামক পদার্থ আছে ভূ-গর্ভস্থ থেকে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের কারণে তা পানির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। প্রতিদিন কৃষিকাজ থেকে শুরু করে নিত্য ব্যবহারের জন্য আমরা যে কোটি কোটি লিটার পানি উত্তোলন করি তাতে ভূগর্ভে যে সাময়িক শূন্যতার সৃষ্টি হয় এতে বায়ু এবং অক্সিজেন মিশ্রিত পানির সাথে আর্সেনিক মিশে যাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে আর্সেনিক দূষণ।
আর্সেনিকের প্রকাশ: ১৯৭৮ সালে ভারতে সর্বপ্রথম আর্সেনিক দূষণের খবর পাওয়া যায়। ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ পরগনার কোনো কোনো এলাকায় মানুষের দেহে আর্সেনিকের প্রভাব চোখে পড়ে। পরবর্তীতে তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সনাক্ত করা হয়।
বিষক্রিয়ার লক্ষণ: মানুষের দেহে আর্সেনিকের লক্ষণ তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ পায় না। অনেক ক্ষেত্রে এর লক্ষণ প্রকাশ পায় ৬ মাস বা তারও পরে। পানিতে কি পরিমাণ আর্সেনিক আছে তার উপর ভিত্তি করে এর বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। বেশি মাত্রায় আর্সেনিক মিশ্রিত পানি অনেক দিন যাবত পান করলে এর লক্ষণ প্রকাশ পায় দ্রুত। প্রথমে দেহে কিংবা হাতের তালুতে বাদামী ছোপ দেখা যায়। পরবর্তীতে হাতের আঙ্গুলগুলোয় পচন ধরে। অনেক সময় আর্সেনিকের প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের পায়ের তালুর চামড়া পুরু হয়ে যায় এবং আঙ্গুলগুলোও বেঁকে যায়। আর্সেনিক আক্রান্ত ব্যক্তি ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে। আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর জিহ্বা, মাড়ি, ঠোঁটে লালভাব দেখা যায়। ক্ষুধামন্দা, খাদ্যে অরুচি এবং বমিবমি অনুভব করে। ধীরে ধীরে হৃদযন্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মানুষের রক্তে শ্বেত ও লোহিত কণিকার পরিমাণ কমে যায়। অনেক সময় রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত এবং গর্ভবতীদের ভ্রুনের মারত্মক ক্ষতি হয়।
প্রতিকার ও পদক্ষেপ: আর্সেনিক বিষক্রিয়া থেকে মুক্তির জন্য আপাতত প্রতিরোধক ব্যবস্থাই সবচেয়ে উপযোগী। বিজ্ঞানীরা আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা পদ্ধতি আজও আবিষ্কার করতে পারেনি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে ০.০৫ মিলিগ্রাম আর্সেনিক মানুষের দেহের জন্য সহনীয় বলা হলেও বর্তমান রিপোর্টে বলা হয়েছে বাংলাদেশের জন্য এ মাত্রা ০.০১ মিলি গ্রামের বেশি হলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে। তাই প্রতিরোধ ও প্রতিকারের দিকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। গবেষণায় দেখা যায় কম গভীরতা সম্পন্ন নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বেশি। বিশেষ করে ১০০-২০০ মিটার গভীরতায় আর্সেনিকের উপস্থিতি কম। আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে-
- গভীর নলকূপের পানি খাবার এবং রান্নার কাজে ব্যবহার করতে হবে।
- বৃষ্টির পানিতে আর্সেনিক থাকেনা। তাই বৃষ্টির পানি জমিয়ে রেখে ব্যবহার করতে হবে।
- রেডিও টেলিভিশন ও গ্রাম্য আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর্সেনিক সম্পর্কে সচেতন করা।
- পুকুর এবং খাল-বিলের পানিতে আর্সেনিক থাকেনা এ ক্ষেত্রে পুকুরে, খাল বা বিলের পানি ছেঁকে ২০ মিনিট ফুটিয়ে পান করতে হবে।
- আর্সেনিক আক্রান্ত গ্রামে নতুন নতুন জলাশয় বা পুকুর খনন করে পানির ব্যবস্থা করতে হবে।
- সরকারি সহায়তার মাধ্যমে আর্সেনিক বিশোধন প্ল্যান্ট স্থাপন করা।
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় পর পর নলকূপের পানি পরীক্ষা করতে হবে।
- বালতি, কলসি এবং SOES, CSIR-এর যৌথ প্রচেষ্টায় উদ্ভাবিত ফ্লাই এ্যাশ দিয়ে ফিল্টারের মাধ্যমে পানি বিশুদ্ধ করা।
- আর্সেনিকযুক্ত নলকূপগুলোকে লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করে সেগুলো থেকে পানি পান বন্ধ করে দিতে হবে।
- আর্সেনিক কোনো সংক্রামক বা ছোঁয়াছে রোগ নয় তাই আতঙ্কিত না হয়ে চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ নিতে হবে।
আমাদের করণীয়: আর্সেনিক যেহেতু ছোঁয়াছে রোগ নয় তাই আতঙ্কিত না হয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং গ্রাম পর্যায়ে আর্সেনিক থেকে মুক্ত থাকার পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারি এবং বেসরকারি সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।
উপসংহার: খাবার পানির মাধ্যমে আর্সেনিক মানুষের শরীরে প্রবেশ করে, তাই আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে। যক্ষ্মা, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি রোগের মতো এ রোগকেও নির্মূল করার পদক্ষেপ নিতে হবে। জনগণকে সচেতন হতে হবে এবং আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় সরকারকে নিরাপদ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।