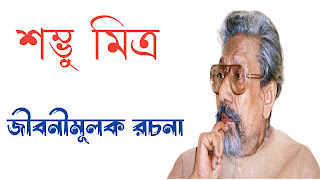জীবনী মূলক রচনা লেবেলটি সহ পোস্টগুলি দেখানো হচ্ছে৷ সকল পোস্ট দেখান
জীবনী মূলক রচনা লেবেলটি সহ পোস্টগুলি দেখানো হচ্ছে৷ সকল পোস্ট দেখান
মঙ্গলবার, ২৯ আগস্ট, ২০২৩
জন্ম ও পারিবারিক পরিচয় :– বাংলা তথা ভারতীয় নাট্য জগতের কিংবদন্তি ব্যাক্তিত্ব শম্ভু মিত্রের জন্ম হয় ১৯১৫ সালে ২২ আগস্ট । তার পিতার নাম শরৎ কুমার মিত্র এবং মাতা শতদল বাসিনী দেবী । শম্ভু মিত্রের পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলি জেলায় । কিন্তু কলকাতায় ভবানীপুরে মাতামহ আদিনাথ বসুর বাড়িতেই তার জন্ম হয় । ১৯৪৫ সালে তিনি প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রর সঙ্গে পরিনয়সূত্রে আবদ্ধ হন ।
ছাত্রজীবন :– শম্ভু মিত্রের প্রথম জীবনের পড়াশোনা শুরু হয় চক্রবেরিয়া মিডল ইংলিশ স্কুলে । এরপরে তিনি বালিগঞ্জ গভর্মেন্ট স্কুলে ভরতি হন । বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে এরপর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভরতি হলেও তিনি পড়াশোনা সমাপ্ত করেননি ।
নাট্যজীবন :– ১৯৩৯ সালে " রঙমহল " থিয়েটার - এ যোগদানের মাধ্যমে শম্ভু মিত্রের বানিজ্যিক নাট্য মঞ্চে পর্দাপন । এখানেই মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তার । রঙমহল বন্ধ হয়ে গেলে প্রথমে তিনি যোগদেন " মিনাভায় " । সেখানে অল্পদিন থেকে তারপর যোগদেন " নাট্য নিকেতন " এ । নাট্য নিকতনে " কালিন্দী " নাটকে অভিনয়ের সূত্রে সে যুগের প্রতি তজশা নাট্য ব্যক্তিত্ব শিশির কুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে তার আলাপ হয় । পরবর্তীকালে শিশির কুমার ভাদুড়ী প্রযোজিত " আলমগীর " নাটকে অভিনয় করলেও সম্পূর্ণ নতুন এক নাট্যঘরানা তৈরীতে উদ্যোগী হন তিনি । এরপর নাট্যনিকেতন ও বন্ধ হয়ে গেলে তিনি " শ্রী রঙ্গম " এ যোগ দেন । কিন্তু পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে শম্ভু মিত্র একাত্ম হতে পারছিলেন না । এই পর্বেই ১৯৪২ সালের শেষ দিকে বিনয় ঘোষ এবং বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে ফ্রাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ হয়ে তিনি যোগদেন " ভারতীয় গননাট্য সংঘ " এ । ১৯৪৪ এ " নবান্ন " নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের যে নবযুগের সূচনা হয় তাতে অভিনেতা ও সহ পরিচালক হিসেবে শম্ভু মিত্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শুধু রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের পরিবর্তে স্বাধীন এবং মুক্তচিন্তা সমৃদ্ধ নাটকে অভিনয়ের লক্ষ্য শম্ভু মিত্র গণনাট্য ত্যাগ করেন ।
[ ] ১৯৪৮ সালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে শম্ভু মিত্র গড়ে তোলেন তার নিজের নাট্য দল " বহুরূপী " । ১৯৫০ - এ অভিনীত হয় " ছেড়া তার " এবং উলুখাগরা । ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত " বহুরূপী " প্রযোজনায় সফোক্লিস , হেনরিক ইবসেন , তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যকারের রচনা তার পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় । শম্ভু মিত্র বাংলা রঙ্গ মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ কে নতুনভাবে আবিষ্কার করেন – " রক্তকরবী " , চার অধ্যায় , বিসর্জন , রাজা ইত্যাদি একের পর এক রবীন্দ্রনাটকের অসামান্য উপস্থাপনা বাংলা নাটকের ইতিহাসে মাইলফলক । অভিনেতা ও পরিচালক শম্ভু মিত্রের মতোই নাট্যকার শম্ভু মিত্রও বাংলা নাটকে স্মরনীয় । চাঁদ বনিকের পালা ইত্যাদি অসামান্য নাটকের রচনাকারও তিনি । এছাড়া তিনি নাটক বিষয়ক বেশ কয়েকটি বইও লিখেছেন । অভিনয় , নাট্য মঞ্চ , প্রসঙ্গ নাট্য , ইত্যাদি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য । ১৯৭০ সালে একটি আর্ট কম্পেলেক্স নির্মাণের উদ্দেশ্যে তিনি " বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চ সমিতি " গঠন করেন । যদিও পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হয়নি ।
[ ] কন্যা শাওলী মিত্রের নাট্যসংস্থা " পঞ্চম বৈদিক " এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি । জীবনের শেষ পর্যায়েও এই সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন ।
আবৃত্তি :– একজন স্বনামধন্য আবৃত্তিকার হিসেবে শম্ভু মিত্রের পরিচিতি ছিল সর্বব্যাপী । তার কণ্ঠে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের " মধুবংশীর গলি " আজও অমর । " রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ " , দিনান্তের প্রণাম , এই দুটি তার অতিপ্রসিদ্ধ বাংলা কবিতা আবৃত্তির রেকর্ড ।
চলচ্চিত্র :– কেবলমাত্র নাটক নয় , চলচ্চিত্রেও তিনি অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন । মানিক , শুভ বিবাহ , পথিক , অভিযাত্রী , ধাত্রী দেবতা , আবত , মরনের পারে , ইত্যাদি তার অভিনীত কিছু বিখ্যাত চলচ্চিত্র । খাজা আহমেদ আব্বাসের পরিচালনায় " ধরতি কে লাল " হিন্দি ছবিটির সহকারী পরিচালক ছিলেন তিনি ।
সম্মান ও স্বীকৃতি :– নাট্য জগতে তার অসামান্য অবদানের জন্য শম্ভু মিত্র স্বীকৃতিও পেয়েছেন অনেক । ১৯৭৬ সালে তিনি পান " ম্যাগসেস পুরষ্কার " । ওই বছরই ভারত সরকার তাকে " পদ্মভূষণ " উপাধিতে ভূষিত করে । ১৯৮৩ সালে বিশ্বভারতী তাকে " দেশিকোওম " উপাধি দেয় । যাদব পুর বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সাম্মানিক ডি. লিট . উপাধিতে ভূষিত করে ।
জীবনবসান :– ১৯৯৭ সালে ১৯ মে কলকাতায় নিজের বাসভবনে শম্ভু মিত্র প্রয়াত হন ।
ছাত্রজীবন :– শম্ভু মিত্রের প্রথম জীবনের পড়াশোনা শুরু হয় চক্রবেরিয়া মিডল ইংলিশ স্কুলে । এরপরে তিনি বালিগঞ্জ গভর্মেন্ট স্কুলে ভরতি হন । বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে এরপর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভরতি হলেও তিনি পড়াশোনা সমাপ্ত করেননি ।
নাট্যজীবন :– ১৯৩৯ সালে " রঙমহল " থিয়েটার - এ যোগদানের মাধ্যমে শম্ভু মিত্রের বানিজ্যিক নাট্য মঞ্চে পর্দাপন । এখানেই মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তার । রঙমহল বন্ধ হয়ে গেলে প্রথমে তিনি যোগদেন " মিনাভায় " । সেখানে অল্পদিন থেকে তারপর যোগদেন " নাট্য নিকেতন " এ । নাট্য নিকতনে " কালিন্দী " নাটকে অভিনয়ের সূত্রে সে যুগের প্রতি তজশা নাট্য ব্যক্তিত্ব শিশির কুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে তার আলাপ হয় । পরবর্তীকালে শিশির কুমার ভাদুড়ী প্রযোজিত " আলমগীর " নাটকে অভিনয় করলেও সম্পূর্ণ নতুন এক নাট্যঘরানা তৈরীতে উদ্যোগী হন তিনি । এরপর নাট্যনিকেতন ও বন্ধ হয়ে গেলে তিনি " শ্রী রঙ্গম " এ যোগ দেন । কিন্তু পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে শম্ভু মিত্র একাত্ম হতে পারছিলেন না । এই পর্বেই ১৯৪২ সালের শেষ দিকে বিনয় ঘোষ এবং বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে ফ্রাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ হয়ে তিনি যোগদেন " ভারতীয় গননাট্য সংঘ " এ । ১৯৪৪ এ " নবান্ন " নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের যে নবযুগের সূচনা হয় তাতে অভিনেতা ও সহ পরিচালক হিসেবে শম্ভু মিত্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শুধু রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের পরিবর্তে স্বাধীন এবং মুক্তচিন্তা সমৃদ্ধ নাটকে অভিনয়ের লক্ষ্য শম্ভু মিত্র গণনাট্য ত্যাগ করেন ।
[ ] ১৯৪৮ সালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে শম্ভু মিত্র গড়ে তোলেন তার নিজের নাট্য দল " বহুরূপী " । ১৯৫০ - এ অভিনীত হয় " ছেড়া তার " এবং উলুখাগরা । ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত " বহুরূপী " প্রযোজনায় সফোক্লিস , হেনরিক ইবসেন , তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যকারের রচনা তার পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় । শম্ভু মিত্র বাংলা রঙ্গ মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ কে নতুনভাবে আবিষ্কার করেন – " রক্তকরবী " , চার অধ্যায় , বিসর্জন , রাজা ইত্যাদি একের পর এক রবীন্দ্রনাটকের অসামান্য উপস্থাপনা বাংলা নাটকের ইতিহাসে মাইলফলক । অভিনেতা ও পরিচালক শম্ভু মিত্রের মতোই নাট্যকার শম্ভু মিত্রও বাংলা নাটকে স্মরনীয় । চাঁদ বনিকের পালা ইত্যাদি অসামান্য নাটকের রচনাকারও তিনি । এছাড়া তিনি নাটক বিষয়ক বেশ কয়েকটি বইও লিখেছেন । অভিনয় , নাট্য মঞ্চ , প্রসঙ্গ নাট্য , ইত্যাদি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য । ১৯৭০ সালে একটি আর্ট কম্পেলেক্স নির্মাণের উদ্দেশ্যে তিনি " বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চ সমিতি " গঠন করেন । যদিও পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হয়নি ।
[ ] কন্যা শাওলী মিত্রের নাট্যসংস্থা " পঞ্চম বৈদিক " এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি । জীবনের শেষ পর্যায়েও এই সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন ।
আবৃত্তি :– একজন স্বনামধন্য আবৃত্তিকার হিসেবে শম্ভু মিত্রের পরিচিতি ছিল সর্বব্যাপী । তার কণ্ঠে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের " মধুবংশীর গলি " আজও অমর । " রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ " , দিনান্তের প্রণাম , এই দুটি তার অতিপ্রসিদ্ধ বাংলা কবিতা আবৃত্তির রেকর্ড ।
চলচ্চিত্র :– কেবলমাত্র নাটক নয় , চলচ্চিত্রেও তিনি অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন । মানিক , শুভ বিবাহ , পথিক , অভিযাত্রী , ধাত্রী দেবতা , আবত , মরনের পারে , ইত্যাদি তার অভিনীত কিছু বিখ্যাত চলচ্চিত্র । খাজা আহমেদ আব্বাসের পরিচালনায় " ধরতি কে লাল " হিন্দি ছবিটির সহকারী পরিচালক ছিলেন তিনি ।
সম্মান ও স্বীকৃতি :– নাট্য জগতে তার অসামান্য অবদানের জন্য শম্ভু মিত্র স্বীকৃতিও পেয়েছেন অনেক । ১৯৭৬ সালে তিনি পান " ম্যাগসেস পুরষ্কার " । ওই বছরই ভারত সরকার তাকে " পদ্মভূষণ " উপাধিতে ভূষিত করে । ১৯৮৩ সালে বিশ্বভারতী তাকে " দেশিকোওম " উপাধি দেয় । যাদব পুর বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সাম্মানিক ডি. লিট . উপাধিতে ভূষিত করে ।
জীবনবসান :– ১৯৯৭ সালে ১৯ মে কলকাতায় নিজের বাসভবনে শম্ভু মিত্র প্রয়াত হন ।
সমার্থক বিশেষিত নাম : মহাত্মা, মহাত্মা গান্ধী, বাপুজী, গান্ধিজী। ভারত নামক রাষ্ট্রের জনক হিসাবে স্বীকৃত।
১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২রা অক্টোবরে গুজরাটের সমুদ্র-উপকূলীয় শহরে পোরবন্দরের পৈত্রিক বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন হিন্দু মোধ গোষ্ঠীর। ইনি পোরবন্দর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। মায়ের নাম পুতলি বাই। ইনি ছিলেন প্রণামী বৈষ্ণব গোষ্ঠীর কন্যা। পিতা করমচাঁদের চতুর্থ স্ত্রী। উল্লেখ্য এঁর আগের তিনজন স্ত্রী সন্তান প্রসবকালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।
১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১৩ বছর বয়সে ইনি তাঁর বাবা মায়ের পছন্দে ১৪ বৎসর বয়সী কস্তুর বাইকে বিয়ে করেন। এঁদের চার পুত্র সন্তান জন্মেছিল। এঁদের নাম ছিল যথাক্রমে– হরিলাল গান্ধী (জন্ম ১৮৮৮), মনিলাল গান্ধী (জন্ম ১৮৯২), রামদাস গান্ধী (জন্ম ১৮৯৭) এবং দেবদাস গান্ধী (জন্ম ১৯০০) সালে।
১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় (ম্যাট্রিকুলেশন ) পাশ করেন রাজকোট হাইস্কুল থেকে। এরপর কিছুদিন তিনি গুজরাটের ভবনগরের সামালদাস কলেজ ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করেন। ১৮৮৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ইনি ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে ভর্তি হন। উল্লেখ্য ইংল্যান্ডে যাবার আগে জৈন সন্ন্যাসী বেচার্জীর সামনে তিনি তার মায়ের কাছে শপথ করেছিলেন যে, তিনি কখনো মাংস, মদ খাবেন না এবং হিন্দু নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করে চলবেন। এই কারণে তিনি লন্ডনের গুটি কয়েক নিরামিষভোজী খাবারের দোকানে আহর করতেন। এই সূত্রে তিনি নিরামিষভোজী সংঘে যোগ দেন এবং ওই সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি এই সংঘের একটি স্থানীয় শাখাও প্রচলন করেন। নিরামিষভোজী অনেক সদস্যই আবার থিওসোফিক্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। উল্লেখ্য ১৮৭৫ সালে এই সংঘটি স্থাপিত হয়েছিল। এই সংঘে বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্মীভিত্তিক সাহিত্য পড়ানো হত। এই সংঘের অনুপ্ররণায় তিনি ভগবত গীতা পাঠ করেছিলেন। পরে তিনি খিষ্টান, বৌদ্ধ, ইসলামসহ অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা করেন।
১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হন এবং জুন মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে দেশে ফিরে ইনি তাঁর মৃত্যু সংবাদ পান। ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করার জন্য, তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কিছু লোক, তাঁকে জাতিচ্যুতের রায় দিয়েছিলেন। এ কারণে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল।
প্রথমে ইনি বোম্বাই আদলতে আইন ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু লাজুক থাকার কারণে ইনি এই আদালতে বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেন নি। এরপর ইনি রাজকোটে ফিরে আসেন। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি এক বছরের জন্য Dada Abdulla Co. নামক একটি ভারতীয় কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে যান। এই কোম্পানির অংশীদার আব্দুল করিম জাভেরি তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত অফিসের মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য নিয়োগ দিয়েছিলেন। এরপর প্রায় ২১ বৎসর তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে কাটান।
তিনি নাটালের সুপ্রিম কোর্টে সর্বপ্রথম ভারতীয় আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত হন। সেসময় দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ভোটাধিকার ছিল না। এই অধিকার আদায়ের বিল উত্থাপিত হলে, তা আদালত বাতিল করে দেয়। এই বিষয়টির সূত্রে তিনি সে সেদেশের ভারতীয়দেরকে অধিকার সচেতন করে তুলেছিল। ১৮৯৪ সালে তাঁর নেতঋত্বে নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।
দক্ষিণ আফ্রিকায়, ১৮৯৫ দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে প্রথমেই তিনি ভারতীয় ও কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শেতাঙ্গদের বৈষম্য আচরণ লক্ষ্য করেন। ১৮৯৫ সালে কিছু ঘটনায় তাঁকে ক্রমে ক্রমে প্রতিবাদী করে তোলে। এখানে তিনি একদিন ডারবানের আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট তার পাগড়ি সরিয়ে ফেলতে বলেন। গান্ধী তা অগ্রাহ্য করেন এবং এই কারণে আদালত কক্ষ থেকে ক্ষোভে বেরিয়ে পড়েন। পিটার ম্যারিজবার্গের একটি ট্রেনের ভ্রমণ করার সময় প্রথম শ্রেণীর বৈধ টিকিট থাকা স্বত্ত্বেও, প্রথম শ্রেণীর কামড়া থেকে তৃতীয় শ্রেণীর কামড়ায় যেতে বাধ্য করা হয়। স্টেজকোচে ভ্রমণের সময় এক ইউরোপীয় যাত্রীকে জায়গা না দেওয়ার জন্য করে দেয়ার জন্য, তাঁকে ফুট বোর্ডে চড়তে বলা হলে, তিনি তা অস্বীকার করেনি।
১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সংক্ষিপ্ত সফর করেন। এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকার নিয়ে ভারতে আন্দোলন করেন। এই কারণে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারিতে যখন তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে আবার দক্ষিণ আফ্রিকা যান, তখন এই সময় প্রবাসী ভারতীয়দের দ্বারা নেতা হিসাবে সম্বর্ধনা পান।
১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বেয়ার যুদ্ধের সময় ইনি ভারতীয়দের দ্বারা একটি এ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গঠন করেন। এই কারণে ইনি যুদ্ধ পদক লাভ করেন। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। এই সময় ট্র্যান্সভালে এশীয়দের বিরুদ্ধে আইন প্রবর্তনের বিপক্ষে আন্দোলন করেন। এই কারণে ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রবাসী ভারতীয়দের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে, আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যান। এবার ইনি ট্র্যান্সভালে সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত হন। ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দের দিকে জোহান্সবার্গে প্লেগ দেখা দিলে তিনি একটি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে জুলু বিদ্রোহ শুরু হলে, আহতদের সেবার জন্য একটি ভারতীয় বাহিনী তৈরি করে, সেবা প্রদান করেন।
১৯০৬ সালে ট্র্যান্সভাল সরকার উপনিবেশের ভারতীয়দের নিবন্ধনে বাধ্য করানোর জন্য একটি আইন পাশ করে। ১১ই সেপ্টেম্বর জোহানেসবার্গের এক সভায় তিনি সবাইকে এই আইন বর্জন করতে বলেন। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে নিষ্ক্রিয় আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। এ সময় আইন অম্যান্য করা, নিজেদের নিবন্ধন কার্ড পুড়িয়ে ফেলাসহ বিভিন্ন কারণে অনেক ভারতীয়কে বন্দী করা হয়। একই কারণে অনেক ভারতীয় হতাহত হন। শান্তিকামী ভারতীয়দের উপর এরূপ নিগীড়নমূলক আচরণের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার স্থানীয় সাধারণ মানুষও প্রতিবাদ করা শুরু করে। সরকার ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে ট্র্যান্সভাল ত্যাগ করার জন্য আদেশ জারি করে। কিন্তু তিনি এই আদেশ অগ্রাহ্য করলে, তাঁর দুই মাসের কারাদণ্ড হয়। পরে জেনারেল স্মার্টস তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে একটি আপোষ রফায় আসেন এবং তাঁর কারাদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করেন। এই আপোষের কারণে ক্ষুব্ধ ভারতীয় পাঠানরা তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেন। পরে স্মার্টস তাঁর আপোষ নাকচ করলে, ইনি পুনরায় নিষ্ক্রিয় আন্দোলন শুরু করেন। এই কারণে ইনি দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন।
১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে ডেপুটেশনে তিনি ইংল্যান্ড যান।নভেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জাহাজে ফিরবার সময়, তাঁর জীবনাদর্শ ও রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কিত বই স্বরাজ রচনা করেন। এই গ্রন্থের অনেকেই সমালোচনা করেছিলেন। তিনি ট্র্যান্সভালে জোহানিসবার্গের নিকট নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মীদের পরিবারের কর্মসসংস্থানের জন্য তলস্তয় নামক একটি খামার স্থাপন করেছিলেন। এই ফার্মের জন্য হেরম্যান কালেনবাক নামক একজন জার্মান স্থপতি এই খামারের জন্য ১১০০ একর জমি দান করেছিলেন।
১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ইনি ইউরোপীয় পোশাক এবং দুধ পরিত্যাগ করেন। এই সময় থেকে তিনি শুকনো ও তাজা ফল খেয়ে জীবন ধারণের অভ্যাস করা শুরু করেন। এছাড়া সপ্তাহে ১ দিন অভ্যাস করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ভারতীয়দের উপর মাথাপিছু ৩ পাউন্ড কর ধার্য করে। এই করারোপের প্রতিবাদে গান্ধীজী আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন ২,০৪৭ জন পুরুষ, ১২৭ জন স্ত্রীলোক এবং ৫৭ জন ছেলেমেয়ে। এঁরা আন্দোলন করার জন্য ট্র্যান্সভালে প্রবেশ করলে, সরকার গান্ধীজীকে গ্রেফতার করে। এই আন্দোলনের কারণে তিনি দুই দফায় ৯ মাস ও ৩ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। এরপর তিনি ইংল্যান্ডে যান।
১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেখানে ভারতীয়দের দ্বারা একটি এ্যাম্বুলেন্স বাহিনী তৈরি করেছিলেন। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের সহায়তা করার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কাইসার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক প্রদান করে। এরপর ইনি ভারতে ফিরে আসেন এবং মে মাসে আহমেদাবাদ সবরমতী নদীর তীরে সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপন করেন। ১৯১৫ -১৬ খ্রিষ্টাব্দে ইনি রেলপথে ভারত এবং বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার) ভ্রমণ করেন।
১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের বিদেশ প্রেরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সাফল্য লাভ করেন। এই বৎসরেই চরকায় সুতা কেটে সেই সুতা থেকে কাপড় তৈরির ধারণা লাভ করেন। এপ্রিল মাসে বিহারের চম্পাবরণে নীলচাষীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। পরে তাঁকে মুক্তিও দেওয়া হয়। এরপর তিনি বিহার সরকার কর্তৃক রায়তদের অবস্থা অনুসন্ধান কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন।
১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে আহমেদাবাদ বস্ত্র কারখানায় শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিকদের নিয়ে আম্দোলন করেন। এই আন্দোলন সহজে মিটমাট হওয়ার জন্য উপবাসসহ প্রার্থনা করেন। এরপর শস্যহানির জন্য বোম্বাই জেলার খাজনা মওকুফের জন্য সত্যাগ্রহ করেন। দিল্লীতে ভাইসরয়ের যুদ্ধ পরিষদের সভায় তিনি হিন্দিতে বক্তৃতা দেন। পরে যুদ্ধে যোগদানের জন্য লোক সংগ্রহের জন্য কয়রা জেলা ভ্রমণ করেন।
১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে রাউটাল বিল বাতিলের জন্য দরখাস্ত করেন। এপ্রিল মাসে সর্বভারতীয় সত্যগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়, এবং হরতাল পালিত হয়। এরপর পাঞ্জাবে তাঁর প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে, তিনি পাঞ্জাবে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এই কারণে দিল্লী যাওয়ার পথে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৩ই এপ্রিল তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধীজী সবরমতী আশ্রমে ৩ দিনের উপবাস করেন। ১৪ই এপ্রিল তারিখে নদিয়াদে স্বীকার করেন যে, সত্যাগ্রহ করে তিনি হিমালয়তূল্য ভুল করেছেন। এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে গুজরাটি ভাষায় নবজীবনপত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। উল্লেখ্য এই পত্রিকাটি পরে হিন্দি ভাষাতেই প্রকাশিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অক্টোবর মাসে তাঁর সম্পাদনায় ইংরেজি পত্রিকা 'ইয়ং ইন্ডিয়া' সম্পাদনা শুরু করেন। নভেম্বর মাসে দিল্লীতে নিখিল ভারত খিলাফত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং সভার সভাপতিত্ব করেন গান্ধীজী। এই সময় মনটেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার গ্রহণ করার জন্য অমৃতসর কংগ্রেসকে পরামর্শ দেন।
১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে তুরস্কের সুলতানের খিলাফত অধিকার রক্ষার জন্য ভাইসরয়ের কাছে ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন। এই বৎসরে ভাইসরয়ের কাছে কাইসার-ই-হিন্দ পদক, জুলু পদক ও বুর যুদ্ধ পদক প্রত্যার্পণ করেন। ডিসেম্বর মাসে নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশন ঘোষণা করা হয়।
১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাঝে মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাহী দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। গুজরাটে তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস স্বরাজের লক্ষ্যকে সামনে রেখে নতুন সংবিধান গ্রহণ করেন। একই সাথে টোকেন ফি দিতে রাজি হওয়া যে কোন ব্যক্তির জন্য দলের সদস্যপদ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।
১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ভাইসরয়কে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, গুজরাটের বরদৌলিতে সত্যাগ্রহ অভিযান চালনা করা হবে। কিন্তু ৫ই ফেব্রুয়ারিতে উত্তর প্রদেশের চৌরিচোরাতে জনতা ২১জন কনস্টেবল ও একজন সাব ইন্সপেক্টরকে অগ্নিদগ্ধ করে মেরে ফেলেন। এই সহিংস ঘটনার জন্য টানা ৫ দিন উপবাস করেন। এরপর সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিত্যাগ করেন।
১৯২২ সালের ১০ মার্চ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৮ মার্চে বিচারে তাঁকে ছয় বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।
১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে পুনাতে তাঁর এপেনডিসাইটিসের অপারেশন করা হয় এবং ৫ ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৮ই সেপ্টেম্বরের হিন্দু-মুসলিমদের বোধ ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য ২১ দিনের উপবাস করেন। ডিসেম্বর মাসে বেলগাঁও কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।
and ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে নিখিল ভারত সুতাকাটা সমিতি স্থাপিত হয়। নভেম্বর মাসে আশ্রমবাসীদের একজন একটি অপকর্ম করে। এই কারণে গান্ধীজী ৭ দিন 'বদলি উপবাস' করেন। এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Story of my Experiments with Truthনামক গ্রন্থ রচনা শুরু করেন।
১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ঘোষণা করা হয়, ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষ হওয়ার আগে ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রদান না করলে, কংগ্রেস আন্দোলন করবেন। কিন্তু ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। ৩১ ডিসেম্বরে ভারতীয় পতাকার উন্মোচন কারা হয় লাহোরে।
১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি লাহোর মিলিত হয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দিনটিকে ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উৎযাপন করে। ফেব্রুয়ারি মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলনের একনায়ক হিসাবে নিযুক্ত হন। মার্চ মাসের শুরুতে, ভাইসরয়কে এক চিঠিতে জানান যে, কংগ্রেসের দাবি না মানলে, তিনি লবণ আইন ভঙ্গ করার আন্দোলন শুরু করবেন। ১২ মার্চ তারিখে এলাহাবাদ থেকে ৪০০ কিলোমিটার হেঁটে ডান্ডি সমুদ্র সৈকতে পৌছান ৬ এপ্রিলে এবং লবণ সংগ্রহ শুরু করেন। এই সময় হাজার হাজার ভারতীয় তাঁর সাথে হেঁটে সাগরের তীরের পৌছান। উল্লেখ্য এটি ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অন্যতম সফল প্রয়াস। ৫ মে তারিখে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিনা বিচারে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। এর ফলে সারা দেশে বিক্ষোভ হলে, প্রায় লক্ষাধিক আন্দোলনকারীকে গ্রফতার করা হয়।
ল্যাঙ্কশায়ারের ডারওয়েনে মহিলা বস্ত্রশ্রমিকদের সাথে, ১৯৩১১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ জানুয়ারিতে তিনি বিনা শর্তে মুক্তি লাভ করেন। এই সময় সরকার গান্ধীর সাথে সমঝোতা করার জন্য লর্ড এডওয়ার্ড আরউইনকে প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে তাঁর অনেকগুলি সাক্ষাৎকার ঘটে এবং অবশেষে আরউইন-গান্ধী চুক্তি সম্পাদিত হয়। এরপর ২৯ আগষ্ট তারিখে তিনি কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে ইংল্যান্ডে গোল-টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য রওনা হন। লণ্ডনে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। ২৬ সেপ্টেম্বরে ল্যাঙ্কশায়ারের ডারওয়েনে মহিলা বস্ত্রশ্রমিকদের সাথে মিছিল করেন। অধিবেশন শেষ ৫ ডিসেম্বরে তিনি লণ্ডন ত্যাগ করেন। ২৮ ডিসেম্বরে বোম্বাই পোঁছুলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিনা বিচারে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। কিছুদিন পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।
১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১ লা জানুয়ারিতে কংগ্রেসর ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ইংরেজের সকল ধরনের রাজনৈতিক অত্যাচারের বন্ধ করার দাবি করা হয়। এবং সাতদিনের মধ্যে এই দাবি না মানলে, আইন-অমান্য আন্দোলন-এর হুমকি দেওয়া হয়। এই সূত্রে সরকার গান্ধীজী, জহরলাল নেহেরু, বল্লভ ভাই প্যাটেল, সুভাষ বসু-সহ বহু নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য, এই সময় সারা দেশে প্রায় ৩২ হাজার নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। ৭ এপ্রিল তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি 'আইন-অমান্য অন্দোলন' প্রত্যাহার করেন। এই কারণে তিনি তীব্রভাবে সমালোচিত হন।
সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা সিদ্ধান্ত অনুসারে হরিজনদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা রহিতকরণের জন্য, ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর তিনি 'আমরণ উপবাস' শুরু করেন। ২৬ সেপ্টেম্বর এই দাবি মেনে নিলে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজি ও হিন্দিতে সাপ্তাহিক হরিজন পত্রিকা স্থাপিত হয়। ৮ই মে থেকে তিনি আত্মশুদ্ধির জন্য ২১ দিনের উপবাস শুরু করেন। এই রাত ৯টার সময় তিনি বিনাশর্তে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। ভারতের জন্য অহিতকর সরকারে সকল আদেশ প্রত্যাহরের জন্য ৯ মে থেকে ৬ সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করেন। ২০শে মে তারিখে উপবাস ভঙ্গ করেন। ২৬শে জুলাই-তে তিনি সত্যাগ্রহ আশ্রম তুলে দেন। ৩০শে জুলাই তারিখে বোম্বাই সরকারকে জানান যে, ৩৩ জন অনুসারী নিয়ে আহমেদাবাদ থেকে রাস পর্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলনের প্রচারণ চালাবেন। এই কারণে ৩১শে জুলাই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৬ই আগষ্ট থেকে অনশন শুরু করলে, ২৩শে আগষ্টে তাঁকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। ৭ই নভেম্বর থেকে তিনি হরিজন উন্নয়নের কাজ শুরু করেন।
১৯৩৪ সালের গ্রীষ্মে তাকে হত্যার জন্য তিনটি ব্যর্থ চেষ্টা চালানো হয়।১৭ সেপ্টেম্বরে এক ঘোষণায় তিনি জানান যে, ১লা অক্টোবর হতে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে পল্লি উন্নয়ন, হরিজন সেবা এবং বুনিয়াদী হস্তশিল্পের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবেন। ২৬ অক্টোবর তিনি নিখিল ভারত পল্লি-শিল্প সমিতি উদ্বোধন করেন।
১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল থেকে মধ্য প্রদেশের সেবাগ্রামে বসতি শুরু করেন এবং এখানে তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবরে তাঁর সভাপতিত্বে বুনিয়াদী কারুশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ইতিপূর্বে রাজকোটের তৎকালীন রাজা শাসন সংস্কারের কিছু অঙ্গীকার করেন এবং পরে তা কার্যকরী না করায়, ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা মার্চ থেকে তিনি আমরণ উপবাস শুরু করেন। পরে ৭ই মার্চে ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপে তিনি উপবাস ভঙ্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে গান্ধী, ১৯৪০
১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে ভাইসরয়ের নিমন্ত্রণের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। অক্টোবর মাসে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার নীতিতে অটল থাকেন। সরকার সংবাদ প্রকাশের পূর্বে পাণ্ডলিপি পরীক্ষণ আদেশ দিলে, হরিজন ও সংশ্লিষ্ট সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর প্রকাশনা বন্ধ করে দেন।
১৯৪১ সালের মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে সকল গণ অসহযোগ আন্দোলন বন্ধের বিনিময়ে সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। ৩০শে ডিসেম্বরে তাঁর অনুরোধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।
১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি থেকে হরিজন ও অন্যান্য পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। এই বৎসরে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স ব্রিটিশ সরকারের শাসন সংস্কারমূলক প্রস্তাব নিয়ে ভারতে আসেন। ২৭শে মার্চ তাঁর সাথে ক্রিপ্সের আলোচনা হয়। ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া প্রস্তাব দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং প্রথম প্লেনে ক্রিপ্সকে দেশে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন। মে মাস থেকে শুরু হয়, 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। ৮ আগষ্টে তিনি বোম্বাই-এ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের ব্যাখ্যা দেন। এই কারণে ৯ই আগষ্টে তাঁকে গ্রেফতার করে পুনার আগা খান প্রাসাদে বন্দী করে রাখা হয়।
১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারিতে তিনি ২১ দিনের উপবাস শুরু করেন। মার্চের ৩ তারিখে অনশন ভঙ্গ করেন। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারিতে গান্ধীজীর পত্নী কস্তরবাই আগাখান প্রাসাদে মৃত্যবরণ করেন। ৬ই মে-তে তিনি বিনা শর্তে মুক্তি পান। সেপ্টেম্বর মাসের ৯ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে গান্ধীজীর আলাপ-আলোচনা হয়।
১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এবং ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্গদেশ ও আসাম ভ্রমণ করেন। এরপর তিনি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। এপ্রিল ও মে মাসে দিল্লী ও সিমলায় ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সাথে রাজনৈতিক আলোচনা হয়। ১৬ই আগষ্টে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে নোয়াখালি জেলায় এবং বিহারে এই দাঙ্গা মারাত্মক রূপ লাভ করে। অক্টোবর মাসে নোয়াখালিতে তিনি কর্মস্থল স্থাপন করে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিতর মৈত্রী-স্থাপনের চেষ্টা করেন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি বিহারে যান। ১৪-১৫ আগষ্টে ভারতবর্ষ বিভাজিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে থাকলে, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরে জনগণের শুভবুদ্ধির আশায় তিনি উপবাস করেন।
১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারিতে দিল্লীতে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। তবে এতে কেউ আহত হন নাই। ৩০ জানুয়ারি তারিখে, দিল্লীর বিরলা ভবনে (বিরলা হাউস) সান্ধ্যা প্রার্থনাসভায় শান্তির বাণী প্রচারের জন্য উপস্থিত হওয়ার প্রাক্কালে নাথুরাম বিনায়ক গোডসে নামক একজন হিন্দু মৌলবাদী তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।
জন্ম ও ছেলেবেলা :– হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮ সালে ১৩ ই নভেম্বর তৎকালীন পাকিস্থানের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোনা মহুকুমার কেন্দুয়ারকুতুব পুরে জন্ম গ্রহণ করেন । তার পিতা শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ এবং মা আয়েশা ফয়েজ । তার পিতা একজন পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন এবং তিনি ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তৎকালীন পিরোজ পুর মহকুমার এস ডি পি ও ( উপ - বিভাগীয় পুলিশ অফিসার ) হিসেবে কর্তব্যরত অবস্থায় শহীদ হন ।
তার পিতা সাহিত্য অনুরাগী মানুষ ছিলেন । তিনি পত্র পত্রিকায় লেখা লেখি করতেন । বগুড়া থাকার সময় তিনি একটি গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন । গ্রন্থের নাম " দ্বীপ নেভা যার ঘরে "। তার মা'র লেখালেখির অভ্যাস না থাকলেও একটি আত্মজীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন যার নাম " জীবন যে রকম " । পরিবারে সাহিত্যমনস্ক আবহাওয়ায় ছিল । তার অনুজ মুহম্মদ জাফর ইকবাল দেশের একজন বিজ্ঞান শিক্ষক এবং কথাসাহিত্যিক ; সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা আহসান হাবিব রম্য সাহিত্যিক এবং কাঠুনিষ্ঠ । তার রচিত উপন্যাস থেকে জানা যায় যে ছোটকালে হুমায়ূন আহমেদের নাম রাখা হয়েছিল শামসুর রহমান ; ডাকনাম কাজল । তার পিতা ( ফয়জুর রহমান ) নিজের নামের সাথে মিল রেখে ছেলের নাম রাখেন শামসুর রহমান । পরবর্তীতে আবার তিনি নিজেই ছেলের নাম পরিবর্তন করে হুমায়ূন আহমেদ রাখেন ।
হুমায়ূন আহমেদের ভাষায় , তার পিতা ছেলে মেয়ে দের নাম পরিবর্তন করতে পছন্দ করতেন । তার ছোট ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবালের নাম আগে ছিল বাবুল এবং ছোটবোন সুফিয়ার নাম ছিল শেফালী । ১৯৬২ - ৬৪ সালে চ্ট্ট গ্রামে থাকাকালীন হুমায়ূন আহমেদের নাম ছিল বাচ্চু ।
শিক্ষা এবং কর্মজীবন :– তার পিতা চাকরি সূত্রে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন বিধায় হুমায়ূন আহমেদ দেশের বিভিন্ন স্কুলে লেখা পড়া করার সুযোগ পেয়েছন । তিনি বগুড়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন এবং রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন । তিনি পরে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই বিজ্ঞানে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন । তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে বি এস সি ( সম্মান ) ও এম এস সি ডিগ্রি লাভ করেন । তিনি মুহসীন হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন এবং ৫৬৪ নং কক্ষে তার ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেন । পরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পলিমার রসায়ন বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচডি লাভ করেন । ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন । এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকা অবস্থায় প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী তোমাদের জন্য ভালোবাসা রচনা করেন । ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন । লেখালেখিতে ব্যাস্ত হয়ে পড়ায় এক সময় তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে দেন । শিক্ষক হিসেবে ছাত্র ছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত জন প্রিয় ছিলেন এই অধ্যাপক ।
শিক্ষা এবং কর্মজীবন :– তার পিতা চাকরি সূত্রে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন বিধায় হুমায়ূন আহমেদ দেশের বিভিন্ন স্কুলে লেখা পড়া করার সুযোগ পেয়েছন । তিনি বগুড়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন এবং রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন । তিনি পরে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই বিজ্ঞানে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন । তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে বি এস সি ( সম্মান ) ও এম এস সি ডিগ্রি লাভ করেন । তিনি মুহসীন হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন এবং ৫৬৪ নং কক্ষে তার ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেন । পরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পলিমার রসায়ন বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচডি লাভ করেন । ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন । এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকা অবস্থায় প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী তোমাদের জন্য ভালোবাসা রচনা করেন । ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন । লেখালেখিতে ব্যাস্ত হয়ে পড়ায় এক সময় তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে দেন । শিক্ষক হিসেবে ছাত্র ছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত জন প্রিয় ছিলেন এই অধ্যাপক ।
সাহিত্যকৃতি :– সগৃহে বৈঠকি আড্ডায় হুমায়ূন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র জীবনে একটি উপন্যাস রচনা রচনার মধ্যে দিয়ে হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য জীবনের শুরু । এই উপন্যাসটির নাম নন্দিত নরকে । ১৯৭১–এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে উপন্যাসটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি । ১৯৭২ - এ কবি সাহিত্যিক আহমেদ ছফার উদ্যেগে উপন্যাসটি খান ব্রাদাস কতৃর্ক গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ।
প্রখ্যাত বাংলা ভাষা শাস্ত্র পন্ডিত আহমেদ শরীফ সত্ব: প্রভৃও হয়ে এ গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিলে বাংলাদেশের সাহিত্যমোদী মহলে কৌতুহল সৃষ্টি হয় । শঙ্খনীল কারাগার তার ২য় গ্রন্থ । মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দুই শতাধিক গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস রচনা করেছেন । তার রচনার প্রধান কয়েককটি বৈশিষ্টের মধ্যে অন্যতম হলো – ' গল্প সমৃদ্ধি ' । এছাড়া তিনি অনায়াসে ও বিশ্বাসযোগ্য ভাবে অতি বাস্তব ঘটনাবলীর অবতারনা করেন যাকে একরূপ যাদু বাস্তবতা হিসেবে গণ্য করা যায় । তার গল্প ও উপন্যাস সংলাপ প্রধান । তার বর্ননা পরিমিত এবং সামান্য পরিসরে কয়েকটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে চরিত্র চিত্রনের অদৃষ্ট পূর্ব প্রতিভা তার রয়েছে । যদিও সমাজচেতনার অভাব নেই তবু লক্ষ্যণীয় যে তার রচনায় রাজনৈতিক প্রণোদনা অনুপস্থিত । সকল রচনাতেই একটা প্রগাঢ শুভবোধ ক্রিয়াশীল থাকে ; ফলে ; নেতিবাচক ;
চরিত্রও তার লেখনীতে লাভ করে দরদী রূপায়ণ । এ বিষয়ে তিনি মার্কিন লেখক স্টেইনবেক দ্বারা প্রভাবিত । অনেক রচনার মধ্যে তার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং উপলদ্ধির প্রচ্ছাপ লক্ষ্য করা যায় । ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস মধ্যহ্ন তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে পরি গণিত । এছাড়া জোছনা ও জননীর গল্প আর একটি বড়ো মাপের রচনা , যা - কিনা ১৯৭১ - এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বন করে রচিত । তবে সাধারনত তিনি সমসাময়িক ঘটনাবলি লিখে থাকেন ।
পারিবারিক জীবন :– হুমায়ূন আহমেদের প্রথমা স্ত্রীর নাম গুলতেকিন আহমেদ । তাদের বিবাহ হয় ১৯৮৩ সালে । এই দম্পতির তিন মেয়ে এবং এক ছেলে । তিন মেয়ের নাম বিপাশা আহমেদ , নোভা আহমেদ, শীলা আহমেদ , এবং ছেলের নাম নুহাশ আহমেদ । অন্য আরেকটি ছেলে অকালে মারা যায় । ১৯৯০ সালে মধ্য ভাগ থেকে শিলার বান্ধবী এবং তার বেশ কিছু নাটক চলচ্চিত্রে অভিনয় করা অভিনেত্রী শাওনের সাথে হুমায়ূন আহমেদের ঘনিষ্টতা জন্মে । এরফলে সৃষ্ট পারিবারিক অশান্তির অবসানকল্পে ২০০৫ - এ গুলতেকিনের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয় এবং ঐ বছরই শাওনকে বিয়ে করেন । এঘরে তাদের তিন ছেলে - মেয়ে জন্ম গ্রহণ করে । প্রথম ভুনিষ্ঠ কন্যাটি মারা যায় । ছেলেদের নাম নিষাদ হুমায়ূন ও নিনিত হুমায়ূন ।
ব্যক্তিগতজীবন :– জীবনের শেষ ভাগে ঢাকা শহরের অভিজাত আবাসিক এলাকা ধানমন্ডির ৩/এ রোড নিমিত দক্ষিণ হওয়া ভবনের একটি ফ্ল্যাটে তিনি বসবাস করছেনন । খুব ভোর বেলা ওঠা তার অভ্যাস ছিল তার , ভোর থেকে সকাল ১০ - ১১ অবধি লিখতেন তিনি । মাটিতে বসে লিখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন । কখনো অবসর পেলে ছবির আঁকতেন । জীবনের শেষ এক যুগ ঢাকার অদূরে গাজীপুরের গ্রামাঞ্চলে ৯০ বিঘা জমির ওপর স্থাপিত বাগান বাড়ী ' নুহাশ পল্লীতে ' থাকতে ভালোবাসতেন তিনি । তিনি বিবরবাসি মানুষ , তবে মজশিলী ছিলেন । গল্প বলতে আর রসিকতা করতে খুব পছন্দ করতেন । তিনি ভনিতাবিহিন ছিলেন । নিরবে মানুষের স্বভাব - প্রকৃতি ,আচার, আচরন , পর্যবেক্ষণ করা তার শখ । তবে সাহিত্য পরিমন্ডলের সঙ্গকিন রাজনীতি বা দলাদলিতে কখনো নিজেকে জড়িয়ে ফেলেননি । তিনি কিছুটা লাজুক প্রকৃতির মানুষ এবং বিপুল জনপ্রিয়তা সত্বেও অন্তরাল জীবন যাপনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন । তবে নিঃসঙ্গতা খুব একটা পছন্দ করতেন না । কোথাও গেলে আত্মীয় - স্বজন , বন্ধু - বান্ধব নিয়ে যেতে পছন্দ করতেন । বাংলাদেশে তার প্রভাব তীব্র ও গভীর ; এজন্য জাতীয় বিষয়ে ও সংকটে প্রায় তার বক্তব্য সংবাদ সমূহ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করে থাকতো । অতুলনীয় জনপ্রিয়তা সত্বেও তিনি অন্তরাল জীবন যাপন করেন এবং লেখালেখি ও চিত্রনির্মাণের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন ।
চলচ্চিত্র নির্মাণ :– টেলিভিশনের জন্য একের পর এক দর্শক নন্দিত নাটক রচনার পর হুমায়ূন আহমেদ ১৯৯০ - এর গোড়ার দিকে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন । তার পরিচালনায় প্রথম চলচ্চিত্র আগুনের পরশমনি মুক্তি পায় ১৯৯৪ সালে । ২০০০ সালে শ্রাবণ মেঘের দিন ও ২০০১ সালে দুই দুয়ারী চলচ্চিত্র দুটি প্রথম শ্রেণীর দর্শক দের কাছে দারুন গ্রহণযোগ্যতা পায় । ২০০৩ - এ নির্মাণ করেন চন্দ্রকথা নামে একটি চলচ্চিত্র । ১৯৭১- এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পেক্ষাপটে ২০০৪ সালে নির্মাণ করেন শ্যামল ছায়া চলচ্চিত্রটি । অতীত ২০০৬ সালে " সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র" বিভাগে একাডেমী পুরস্কার এর জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল । এছাড়াও চলচ্চিত্রটি কয়েকটি আন্তজার্তিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় । তার সব চলচ্চিত্রে তিনি নিজে গান রচনা করেন। ২০১২ সালে তার পরিচালনার সর্বশেষ ছবি ঘেটুপুত্র কমলা ( চলচ্চিত্র ) । এছাড়াও হুমায়ূন আহমেদের লেখা উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র । এর মধ্যে ২০০৬ সালে মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত দুরন্ত , বেলাল আহমেদ পরিচালিত নন্দিত নরকে এবং আবু সাইদ পরিচালিত নিরন্তর । ২০০৭ - এ শাহ আলম কিরণ পরিচালিত সাজঘর এবং তৌকির আহমেদ নির্মাণ করেন বহুল আলোচিত চলচ্চিত্র দারুচিনি দ্বীপ ।
কান্সার ও মৃত্যু :– ২০১১ - এর সেপ্টেম্বর মাসে সিঙ্গাপুরে ডাক্তারী চিকিৎসার সময় তার দেহে মলাশয়ের কান্সার ধরা পড়ে ।তিনি নিউইয়কের মেমোরিয়াল স্লয়ান কেটরিং কান্সার সেন্টারে চিকিৎসা গ্রহণ করেন । তবে টিউমার বাইরে ছড়িয়ে না পড়ায় সহজে তার চিকিৎসা প্রাথমিক ভাবে সম্ভব হলেও অল্প সময়ের মাঝেই তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় । ১২ দফায় তাকে কেমোথেরাপি দেওয়া হয়েছিল । অস্ত্রোপচারের পর তাঁর কিছুটা শারীরিক উন্নতি হলেও , শেষ মুহূর্তে শরীরের অজ্ঞাত ভাইরাস আক্রমন করায় তার অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যায় । কৃত্রিম ভাবে লাইভ সাপোর্টে রাখার পর ১৯ জুলাই ২০১২ তারিখে হুমায়ূন আহমেদ মৃত্যুবরণ করেন । মলাশয়ের কান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ নয় মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ২০১২ সালের ১৯ জুলাই - এ স্থানীয় সময় ১১:২০ মিনিটে নিউ ইয়র্কের বেলেভু হাসপাতালে এই নন্দিত লেখক মৃত্যুবরণ করেন । তাকে নুহাশ পল্লীতে দাফন করা হয় । তার মৃত্যুতে সারা বাংলাদেশে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অভূটপূর্ব আহাজারির সৃষ্টি হয় । তার মৃত্যুর ফলে বাংলা সাহিত্যে ও চলচ্চিত্র অঙ্গনে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয় ।
সমাপ্ত
জগদীশচন্দ্র বসু পৃথিবী-বিখ্যাত এক বাঙালি বিজ্ঞানীর নাম। বাংলাদেশের অতিপ্রাচীন জনপদ বিক্রমপুরে তাঁর পৈতৃক নিবাস। জগদীশচন্দ্র বসুর বাবা ভগবানচন্দ্র বসু এবং মা বামাসুন্দরী দেবী।
ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন শিক্ষিত, অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন্ন, আধুনিক ও স্বাধীনচেতা একজন মানুষ। ভগবানচন্দ্র বসু প্রথম জীবনে স্কুলে শিক্ষকতা করেন ময়মনসিংহের একটি বাংলা স্কুলে। এ ময়মনসিংহেই জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর। পরে ভগবানচন্দ্র বসু চাকরি নেন ব্রিটিশ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে।
ব্রিটিশ সরকারের চাকুরে এ ব্যতিক্রমী মানুষটি চাইতেন ছেলে বড় হয়ে অন্যের গোলাম হবে না। তাই তিনি ছেলেকে দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অবারিত সুযোগ করে দেয়ার জন্য স্কুল জীবনের শুরুতেই ভর্তি করান একটি সাধারণ বাংলা মাধ্যমের স্কুলে।
গ্রামের বাংলা মাধ্যমের এ স্কুলের শিক্ষাই যে তাঁর জীবনের ভবিষ্যতের পাথেয় হয়েছিল, সে অভিজ্ঞতার কথা জগদীশ বলেন,
'শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাংলা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরেজি স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলের দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাসীর পুত্র এবং বাম দিকে এক ধীবরপুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর বৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবত প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে আমার অনুরাগ এইসব ঘটনা হইতেই বদ্ধমূল হইয়াছিল।'
ছোটবেলায় জগদীশের নিত্যদিনের সহচর ছিল একজন ডাকাত সর্দার। বালক জগদীশ প্রতিদিন ওই ডাকাতের কাঁধে চড়ে স্কুলে যায়, আবার স্কুল ছুটির পর ডাকাতের কাঁধে চড়েই বাড়ি ফিরে আসে। ছেলেবেলায় এ ডাকাত সর্দারের কাছ থেকে জগদীশ শোনেন তাঁর যৌবনের অনেক গল্পকথা। ডাকাত সর্দারের অসীম সাহসিকতার কাহিনী শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে বালক জগদীশের মন।
ফরিদপুরের সাধারণ বাংলা স্কুলে ৫ বছর পড়ার পর ১০ বছর বয়সে জগদীশ চলে আসেন কলকাতায়। প্রথমে ভর্তি হন হেয়ার স্কুলে। পরে ভর্তি হন কলকাতার বিখ্যাত সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। এ স্কুল থেকে ১৮৭৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন। এর পর তিনি ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। এ কলেজেই শিক্ষাগুরু হিসেবে পেয়ে যান পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁকে। পদার্থবিজ্ঞানের দুরূহসব তত্ত্বকে খুব সহজে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করাতে ফাদার লাফোঁর জুড়ি ছিল না। তাছাড়া নতুন শিক্ষার্থীদের পদার্থবিজ্ঞানে আগ্রহী করে গড়ে তুলতেও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জগদীশচন্দ্র ফাদার লাফোঁর সাহচর্যেই পদার্থবিজ্ঞানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।
১৮৭৭ সালে এ কলেজ থেকে এফএ পাস করেন এবং ১৮৮০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন।
১৮৮১ সালের জানুয়রি মাসে ক্যামব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে প্রকৃতিবিজ্ঞানে ভর্তি হন জগদীশ। এ কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক লর্ড র্যালে, শারীরতত্ত্ববিদ মাইকেল ফস্টার, ভ্রূণতত্ত্ববিদ ফ্রান্সিস বালফুর, ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক হাগস, শারীরতত্ত্ববিদ ফ্রান্সিস ডারউইন, অধ্যাপক ভাইনসের মতো পৃথিবী-বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে জগদীশ বিজ্ঞানে আরও অধিক উৎসাহী হয়ে ওঠেন।
১৮৮৪ সালে লন্ডনের পড়ালেখা শেষ করে জগদীশ দেশে ফিরে আসেন শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের অভিপ্রায়ে। ১৮৮৫ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু এ পদে তাঁর বেতন নির্ধারণ করা হলো একজন ইউরোপীয় সহকারী অধ্যাপকের এক-তৃতীয়াংশ। সমযোগ্যতাসম্পন্ন একজন ভারতীয়ের বেতন একজন ইউরোপীয়র এক-তৃতীয়াংশ_ জগদীশের পক্ষে এ অন্যায় মেনে নেয়া ছিল অসম্ভব। খুব স্বাভাবিকভাবেই জগদীশ ব্রিটিশদের এ অপমানজনক নিবর্তনমূলক নিয়ম মেনে নেননি। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন তিনি। বিনা বেতনে শিক্ষকতা শুরু করেন জগদীশ। দীর্ঘ ৩ বছর নিরবচ্ছিন্ন প্রতিবাদে অবশেষে পিছু হটতে বাধ্য হয় ব্রিটিশরা। ভারতীয়দের জন্য অমর্যাদাকর নিয়ম রহিত করে ১৮৮৮ সালে। তিন বছরের পাওনা একসঙ্গে পরিশোধ করে ব্রিটিশ সরকার।
প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি জগদীশ পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা শুরু করেন। অল্পদিনেই তিনি সাফল্য পান। অতিক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোর ধর্ম এবং তা উৎপাদন ও ধরার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন তিনি। ১৮৯৫ সালের ১ মে এশিয়াটিক সোসাইটির এক সম্মেলনে গবেষণা প্রবন্ধ পাঠ করেন তিনি। একই বছর কলকাতার টাউন হলে এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এ প্রদর্শনীতে তিনি তাঁর উদ্ভাবিত মাইক্রোওয়েভ দিয়ে লোহার গোলা নিক্ষেপ করেন, পিস্তলের আওয়াজ ফোটান এবং বারুদস্তূপ উড়িয়ে দিতে সক্ষম হন।
বলাবাহুল্য, জগদীশের এ প্রদর্শনীই বর্তমানের রাডার প্রযুক্তির প্রাথমিক ধাপ। জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভাবিত এ মাইক্রোওয়েভ দিয়ে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা সক্ষম ছিল। কিন্তু জগদীশ চেয়েছিলেন এ তরঙ্গের আরও বহুমুখী ব্যবহার।
১৮৯৬ সালের ২৪ জুলাই বোম্বে থেকে জাহাজে করে জগদীশ লন্ডনের উদ্দেশে রওনা করেন। ওই বছরের ২১ সেপ্টেম্বর তিনি ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রদান করেন। এদিন বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন জেজে থমসন, অলিভার লজ, লর্ড কেলভিন প্রমুখ। এটি ছিল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর প্রথম বক্তৃতা।
জগদীশের এ বক্তৃতার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের রাজ্যে বাঙালির যাত্রা শুরু। জগদীশচন্দ্র বসুই প্রথম বাঙালি বিজ্ঞানী, যাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশকে বিজ্ঞানের অঙ্গনে সুপরিচিত করে তোলে। বক্তৃতা শেষে লর্ড কেলভিন ও অলিভার লজ জগদীশচন্দ্রকে ইংল্যান্ডে থেকে কাজ করার আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু জগদীশ রাজী হননি।
জগদীশের প্রায় একই সময় মাইক্রোওয়েভ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন ইতালির বিজ্ঞানী মার্কোনি। ১৯০২ সালে, জগদীশের প্রায় ৭ বছর পর মার্কোনি আটলান্টিকের অপর পারে বিনা তারে বার্তা প্রেরণে সক্ষম হন। তত দিনে জগদীশ পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা ছেড়ে উদ্ভিদবিজ্ঞানে গবেষণা শুরু করেছেন। তিনি উদ্ভিদের স্নায়ু, স্বতঃস্পন্দন, আবেগ, অনুভূতি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।
তাঁর এসব গবেষণার মূলে রয়েছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে ঐক্যের সম্বন্ধ স্থাপন। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে এ ঐক্য অন্বেষণ করতে গিয়ে জগদীশ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বৃক্ষের স্নায়ু আছে। এটি প্রমাণ করতে গিয়ে জগদীশকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের রোষানলেও পড়তে হয়েছে। একজন পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাঁর এ গবেষণাকে অনেকে দেখেছেন অনধিকারচর্চা হিসেবে। কিন্তু জগদীশ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এ বিভেদ মানতে রাজি নন। তাই জগদীশ বলেন, 'পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়ছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ জাতিভেদ প্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।'
জগদীশ দৃঢ়তার সঙ্গে উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান। পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার যে ধারা, তার বিপরীতে তিনি গড়ে তোলেন সম্পূর্ণ নতুন এক ধারা। জগদীশের এ গবেষণার মধ্য দিয়ে আন্তঃবিষয়ী গবেষণার এক অভিনব ধারার দ্বার উন্মোচিত হয়, যার নাম জৈবপদার্থবিজ্ঞান। জগদীশ হয়ে ওঠেন এ ধারার পথিকৃৎ। ইতিহাসে জগদীশচন্দ্র বসু হয়ে ওঠেন প্রথম জৈবপদার্থবিজ্ঞানী।
জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো এতই অভিনব যে, তখনকার বিজ্ঞানীদের পক্ষে তা মেনে নেয়া খুব সহজ ছিল না। এ কারণে তাঁর প্রতিটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রসামগ্রী তৈরির জন্য কোনো রকমের আধুনিক প্রযুক্তি ও সুযোগ-সুবিধা তাঁর ছিল না। তাই টিনের পাত, লোহার চাকতি, কাঠের টুকরা ইত্যাদি অব্যবহৃত অকেজো বস্তুসামগ্রী দিয়ে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সাধারণ কামার-মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি করিয়ে নিতে থাকলেন বিজ্ঞান গবেষণার আধুনিক সব যন্ত্রপাতি। এভাবেই তিনি একে একে তৈরি করেন ৫ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টির যন্ত্র, কোহেরার, কালেকটিং ফানেল, হর্ন এন্টেনা, সমাবর্তক (চড়ষধৎরংবৎ) ও বিশ্লেষক যন্ত্র (অহধষুংবৎ), স্ট্রেন সেল, চৌম্বক-লিভার রেকর্ডার, রেজোন্যান্ট রেকর্ডার, ইলেকট্রিক প্রোব, ফাইটোগ্রাফ, শোষণগ্রাফ (ফটোগ্রাফ), স্বয়ংক্রিয় ফটোগ্রাফ, বাবলার ইনস্ট্রুমেন্ট, প্লান্ট সিসমোগ্রাফ, ক্রেসকোগ্রাফ, চৌম্বক ক্রেসকোগ্রাফ, স্বয়ংক্রিয় ফটোসিনথেসিস রেকর্ডার ইত্যাদি। শোনা যায়, তিনি দুই শতাধিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন।
জগদীশ যখন পৃথিবী-বিখ্যাত বিজ্ঞানী, রবীন্দ্রনাথ তখন অপার সম্ভাবনার এক তরুণ কবি। ১৮৯৭ সালে ইউরোপ জয় করে বিজয়বেশে জগদীশ যখন কলকাতায় ফিরে আসেন, তখন রেলস্টেশনে তাঁকে অভিবাদন জানাতে উপস্থিত ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ। এর কিছুদিন পরে পৃথিবী-বিখ্যাত এ বিজ্ঞানীকে শুভেচ্ছা জানাতে ছুটে যান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে না পেয়ে শুভেচ্ছা স্মারক হিসেবে রেখে আসেন একগুচ্ছ ম্যাগনোলিয়া ফুল আর একটি চিঠি। এর কয়েক দিন পর রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'জগদীশচন্দ্র বসু' শিরোনামের একটি কবিতা। এর পর থেকে তাঁদের বন্ধুত্ব শুরু। রবীন্দ্রনাথ যেমন উৎসাহ দিয়ে বন্ধুর বিজ্ঞান গবেষণায় উজ্জীবিত রাখেন, জগদীশও তেমনি রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করে তোলেন।
ইউরোপে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য অনুবাদ করে তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুদের পড়ে শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা চিঠিতে জগদীশ বলেন, 'তোমার পুস্তকের জন্য আমি অনেক মতলব করিয়াছি। তোমাকে যশোম-িত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তর্জমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারে না। তবে কী করিয়া ঢ়ঁনষরংয করিতে হইবে, এখনও জানি না। চঁনষরংযবৎ-রা ফাঁকি দিতে চায়।' জগদীশ চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিম-লে উঠে আসুক; রবির আলোয় সারা পৃথিবী আলোকিত হোক। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের এক অপূর্ব সেতুবন্ধন হয়েছিল এ দুই মহান ব্যক্তির বন্ধুত্বের মাধ্যমে।
১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার অর্জনের মধ্য দিয়ে জগদীশের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা সফল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এ নোবেল বিজয়ে জগদীশের তাই আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না। এ অনুভূতিতে জগদীশ লেখেন, 'পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্য ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল। দেবতার এই করুণার জন্য কি করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব? চিরকাল শক্তিশালী হও, চিরকাল জয়যুক্ত হও। ধর্মর্ তোমার চিরসহায় হউন।'
রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়, তার সভাপতি ছিলেন স্বয়ং জগদীশচন্দ্র বসু।
১৯১৭ সালের ৩০ নভেম্বর নিজের ৫৯তম জন্মদিনে কলকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নিজ দেশে একটি বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন শুরু হয়।
জগদীশ তাঁর জীবদ্দশায় অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন।
১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ভারত সরকার তাঁকে সিআইই (ঈযধসঢ়রড়হংযরঢ় ড়ভ ঃযব ওহফরধহ ঊসঢ়রৎব) উপাধি, ১৯১২ সালে জগদীশ সিএসআই (ঈড়সঢ়ধহরড়হংযরঢ় ড়ভ ঃযব ংঃধৎ ড়ভ ওহফরধ) উপাধি, ১৯১৭ সালে নাইট উপাধিতে ভূষিত হন তিনি। ১৯২৬ সালে বেলজিয়ামের রাজা জগদীশচন্দ্র বসুকে রাজকীয় কমান্ডার অব দি অর্ডার অব লিওপোল্ড উপাধিতে ভূষিত করেন।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে।
এছাড়া ১৯২০ লন্ডন রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। পৃথিবীর যে কোনো বিজ্ঞানীর জন্যই এটি একটি বিরাট স্বীকৃতি। জগদীশচন্দ্র বসুই হলেন ভারতবর্ষের প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৯ সালে দশমবারের জন্য ইউরোপ যাত্রা করেন এবং ফিনল্যান্ডের বিজ্ঞান সমিতি কর্তৃক সংবর্ধিত হন।
১৯৩৭ সালের ২ নভেম্বর রায়বাহাদুর এএন মিত্রের আমন্ত্রণে সস্ত্রীক গিরিডি যাত্রা করেন। ২৩ নভেম্বর সকাল ৮টায় গিরিডিতে হঠাৎ বাথরুমে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। ২৪ নভেম্বর ভোর ৪টা ১২ মিনিটে গিরিডিতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মরদেহ নিয়ে আসা হয় বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে মরদেহ নিয়ে শেষ যাত্রা শুরু হয়; আর পার্ক সার্কাস ক্রিমেটরিয়ামে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
জগদীশের আজন্ম সাধনা ছিল সত্য অনুসন্ধান। জগদীশ জানতেন সত্যই জ্ঞান। জগদীশ মনে করতেন কবি, ঋষি, বিজ্ঞানী সবাই জ্ঞানের সাধক, সত্যের সাধক। কবি ও বিজ্ঞানীর সত্য অনুসন্ধিৎসার প্রসঙ্গে জগদীশ বলেছেন, 'বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না।'
জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানের পথেই সত্য অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। এ কারণেই তিনি 'বিশ্বাসের সত্য'কে 'বিজ্ঞানের সত্য' দিয়ে যাচাই করে এ দুয়ের ব্যবধান ঘোচাতে চেয়েছেন। বালক বয়সে জগদীশ চেয়েছিলেন উঁচু-নিচুর ব্যবধান ঘোচাতে। তরুণ বয়সে চেয়েছিলেন শাসক আর শোষিতের ব্যবধান ঘোচাতে। পরিণত বয়সে জগদীশের এ চেতনাই যেন পরিপক্ব হয়ে আরও উন্নত হয়ে ধরা দিয়েছিল তাঁর গবেষণায়। এ কারণেই তিনি ঘোচাতে চেয়েছেন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ব্যবধান, বিজ্ঞান-সাহিত্যের ব্যবধান, উদ্ভিদ-প্রাণীর ব্যবধান, এমনকি সপ্রাণ-অপ্রাণের ব্যবধানও। জগদীশের আজন্ম সাধনা ছিল এ ব্যবধান ঘোচানো। এ ব্যবধান ঘোচাতে গিয়ে জগদীশ সাফল্যের এমন এক গগনচুম্বী উচ্চতায় আরোহণ করেছেন, যেখানে খুব কম লোকের পক্ষেই যাওয়া সম্ভব। পৃথিবীর অসাধারণ সফল মানুষের মধ্যেও জগদীশ আলাদা। বাঙালির মধ্যে জগদীশ অনন্য, সবার চেয়ে এগিয়ে। এ কারণেই জগদীশ আজও প্রাসঙ্গিক, জগদীশ আজও গুরুত্বপূর্ণ।
ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন শিক্ষিত, অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন্ন, আধুনিক ও স্বাধীনচেতা একজন মানুষ। ভগবানচন্দ্র বসু প্রথম জীবনে স্কুলে শিক্ষকতা করেন ময়মনসিংহের একটি বাংলা স্কুলে। এ ময়মনসিংহেই জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর। পরে ভগবানচন্দ্র বসু চাকরি নেন ব্রিটিশ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে।
ব্রিটিশ সরকারের চাকুরে এ ব্যতিক্রমী মানুষটি চাইতেন ছেলে বড় হয়ে অন্যের গোলাম হবে না। তাই তিনি ছেলেকে দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অবারিত সুযোগ করে দেয়ার জন্য স্কুল জীবনের শুরুতেই ভর্তি করান একটি সাধারণ বাংলা মাধ্যমের স্কুলে।
গ্রামের বাংলা মাধ্যমের এ স্কুলের শিক্ষাই যে তাঁর জীবনের ভবিষ্যতের পাথেয় হয়েছিল, সে অভিজ্ঞতার কথা জগদীশ বলেন,
'শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাংলা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরেজি স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলের দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাসীর পুত্র এবং বাম দিকে এক ধীবরপুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর বৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবত প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে আমার অনুরাগ এইসব ঘটনা হইতেই বদ্ধমূল হইয়াছিল।'
ছোটবেলায় জগদীশের নিত্যদিনের সহচর ছিল একজন ডাকাত সর্দার। বালক জগদীশ প্রতিদিন ওই ডাকাতের কাঁধে চড়ে স্কুলে যায়, আবার স্কুল ছুটির পর ডাকাতের কাঁধে চড়েই বাড়ি ফিরে আসে। ছেলেবেলায় এ ডাকাত সর্দারের কাছ থেকে জগদীশ শোনেন তাঁর যৌবনের অনেক গল্পকথা। ডাকাত সর্দারের অসীম সাহসিকতার কাহিনী শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে বালক জগদীশের মন।
ফরিদপুরের সাধারণ বাংলা স্কুলে ৫ বছর পড়ার পর ১০ বছর বয়সে জগদীশ চলে আসেন কলকাতায়। প্রথমে ভর্তি হন হেয়ার স্কুলে। পরে ভর্তি হন কলকাতার বিখ্যাত সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। এ স্কুল থেকে ১৮৭৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন। এর পর তিনি ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। এ কলেজেই শিক্ষাগুরু হিসেবে পেয়ে যান পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁকে। পদার্থবিজ্ঞানের দুরূহসব তত্ত্বকে খুব সহজে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করাতে ফাদার লাফোঁর জুড়ি ছিল না। তাছাড়া নতুন শিক্ষার্থীদের পদার্থবিজ্ঞানে আগ্রহী করে গড়ে তুলতেও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জগদীশচন্দ্র ফাদার লাফোঁর সাহচর্যেই পদার্থবিজ্ঞানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।
১৮৭৭ সালে এ কলেজ থেকে এফএ পাস করেন এবং ১৮৮০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন।
১৮৮১ সালের জানুয়রি মাসে ক্যামব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে প্রকৃতিবিজ্ঞানে ভর্তি হন জগদীশ। এ কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক লর্ড র্যালে, শারীরতত্ত্ববিদ মাইকেল ফস্টার, ভ্রূণতত্ত্ববিদ ফ্রান্সিস বালফুর, ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক হাগস, শারীরতত্ত্ববিদ ফ্রান্সিস ডারউইন, অধ্যাপক ভাইনসের মতো পৃথিবী-বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে জগদীশ বিজ্ঞানে আরও অধিক উৎসাহী হয়ে ওঠেন।
১৮৮৪ সালে লন্ডনের পড়ালেখা শেষ করে জগদীশ দেশে ফিরে আসেন শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের অভিপ্রায়ে। ১৮৮৫ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু এ পদে তাঁর বেতন নির্ধারণ করা হলো একজন ইউরোপীয় সহকারী অধ্যাপকের এক-তৃতীয়াংশ। সমযোগ্যতাসম্পন্ন একজন ভারতীয়ের বেতন একজন ইউরোপীয়র এক-তৃতীয়াংশ_ জগদীশের পক্ষে এ অন্যায় মেনে নেয়া ছিল অসম্ভব। খুব স্বাভাবিকভাবেই জগদীশ ব্রিটিশদের এ অপমানজনক নিবর্তনমূলক নিয়ম মেনে নেননি। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন তিনি। বিনা বেতনে শিক্ষকতা শুরু করেন জগদীশ। দীর্ঘ ৩ বছর নিরবচ্ছিন্ন প্রতিবাদে অবশেষে পিছু হটতে বাধ্য হয় ব্রিটিশরা। ভারতীয়দের জন্য অমর্যাদাকর নিয়ম রহিত করে ১৮৮৮ সালে। তিন বছরের পাওনা একসঙ্গে পরিশোধ করে ব্রিটিশ সরকার।
প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি জগদীশ পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা শুরু করেন। অল্পদিনেই তিনি সাফল্য পান। অতিক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোর ধর্ম এবং তা উৎপাদন ও ধরার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন তিনি। ১৮৯৫ সালের ১ মে এশিয়াটিক সোসাইটির এক সম্মেলনে গবেষণা প্রবন্ধ পাঠ করেন তিনি। একই বছর কলকাতার টাউন হলে এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এ প্রদর্শনীতে তিনি তাঁর উদ্ভাবিত মাইক্রোওয়েভ দিয়ে লোহার গোলা নিক্ষেপ করেন, পিস্তলের আওয়াজ ফোটান এবং বারুদস্তূপ উড়িয়ে দিতে সক্ষম হন।
বলাবাহুল্য, জগদীশের এ প্রদর্শনীই বর্তমানের রাডার প্রযুক্তির প্রাথমিক ধাপ। জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভাবিত এ মাইক্রোওয়েভ দিয়ে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা সক্ষম ছিল। কিন্তু জগদীশ চেয়েছিলেন এ তরঙ্গের আরও বহুমুখী ব্যবহার।
১৮৯৬ সালের ২৪ জুলাই বোম্বে থেকে জাহাজে করে জগদীশ লন্ডনের উদ্দেশে রওনা করেন। ওই বছরের ২১ সেপ্টেম্বর তিনি ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রদান করেন। এদিন বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন জেজে থমসন, অলিভার লজ, লর্ড কেলভিন প্রমুখ। এটি ছিল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর প্রথম বক্তৃতা।
জগদীশের এ বক্তৃতার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের রাজ্যে বাঙালির যাত্রা শুরু। জগদীশচন্দ্র বসুই প্রথম বাঙালি বিজ্ঞানী, যাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশকে বিজ্ঞানের অঙ্গনে সুপরিচিত করে তোলে। বক্তৃতা শেষে লর্ড কেলভিন ও অলিভার লজ জগদীশচন্দ্রকে ইংল্যান্ডে থেকে কাজ করার আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু জগদীশ রাজী হননি।
জগদীশের প্রায় একই সময় মাইক্রোওয়েভ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন ইতালির বিজ্ঞানী মার্কোনি। ১৯০২ সালে, জগদীশের প্রায় ৭ বছর পর মার্কোনি আটলান্টিকের অপর পারে বিনা তারে বার্তা প্রেরণে সক্ষম হন। তত দিনে জগদীশ পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা ছেড়ে উদ্ভিদবিজ্ঞানে গবেষণা শুরু করেছেন। তিনি উদ্ভিদের স্নায়ু, স্বতঃস্পন্দন, আবেগ, অনুভূতি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।
তাঁর এসব গবেষণার মূলে রয়েছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে ঐক্যের সম্বন্ধ স্থাপন। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে এ ঐক্য অন্বেষণ করতে গিয়ে জগদীশ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বৃক্ষের স্নায়ু আছে। এটি প্রমাণ করতে গিয়ে জগদীশকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের রোষানলেও পড়তে হয়েছে। একজন পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাঁর এ গবেষণাকে অনেকে দেখেছেন অনধিকারচর্চা হিসেবে। কিন্তু জগদীশ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এ বিভেদ মানতে রাজি নন। তাই জগদীশ বলেন, 'পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়ছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ জাতিভেদ প্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।'
জগদীশ দৃঢ়তার সঙ্গে উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান। পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার যে ধারা, তার বিপরীতে তিনি গড়ে তোলেন সম্পূর্ণ নতুন এক ধারা। জগদীশের এ গবেষণার মধ্য দিয়ে আন্তঃবিষয়ী গবেষণার এক অভিনব ধারার দ্বার উন্মোচিত হয়, যার নাম জৈবপদার্থবিজ্ঞান। জগদীশ হয়ে ওঠেন এ ধারার পথিকৃৎ। ইতিহাসে জগদীশচন্দ্র বসু হয়ে ওঠেন প্রথম জৈবপদার্থবিজ্ঞানী।
জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো এতই অভিনব যে, তখনকার বিজ্ঞানীদের পক্ষে তা মেনে নেয়া খুব সহজ ছিল না। এ কারণে তাঁর প্রতিটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রসামগ্রী তৈরির জন্য কোনো রকমের আধুনিক প্রযুক্তি ও সুযোগ-সুবিধা তাঁর ছিল না। তাই টিনের পাত, লোহার চাকতি, কাঠের টুকরা ইত্যাদি অব্যবহৃত অকেজো বস্তুসামগ্রী দিয়ে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সাধারণ কামার-মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি করিয়ে নিতে থাকলেন বিজ্ঞান গবেষণার আধুনিক সব যন্ত্রপাতি। এভাবেই তিনি একে একে তৈরি করেন ৫ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টির যন্ত্র, কোহেরার, কালেকটিং ফানেল, হর্ন এন্টেনা, সমাবর্তক (চড়ষধৎরংবৎ) ও বিশ্লেষক যন্ত্র (অহধষুংবৎ), স্ট্রেন সেল, চৌম্বক-লিভার রেকর্ডার, রেজোন্যান্ট রেকর্ডার, ইলেকট্রিক প্রোব, ফাইটোগ্রাফ, শোষণগ্রাফ (ফটোগ্রাফ), স্বয়ংক্রিয় ফটোগ্রাফ, বাবলার ইনস্ট্রুমেন্ট, প্লান্ট সিসমোগ্রাফ, ক্রেসকোগ্রাফ, চৌম্বক ক্রেসকোগ্রাফ, স্বয়ংক্রিয় ফটোসিনথেসিস রেকর্ডার ইত্যাদি। শোনা যায়, তিনি দুই শতাধিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন।
জগদীশ যখন পৃথিবী-বিখ্যাত বিজ্ঞানী, রবীন্দ্রনাথ তখন অপার সম্ভাবনার এক তরুণ কবি। ১৮৯৭ সালে ইউরোপ জয় করে বিজয়বেশে জগদীশ যখন কলকাতায় ফিরে আসেন, তখন রেলস্টেশনে তাঁকে অভিবাদন জানাতে উপস্থিত ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ। এর কিছুদিন পরে পৃথিবী-বিখ্যাত এ বিজ্ঞানীকে শুভেচ্ছা জানাতে ছুটে যান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে না পেয়ে শুভেচ্ছা স্মারক হিসেবে রেখে আসেন একগুচ্ছ ম্যাগনোলিয়া ফুল আর একটি চিঠি। এর কয়েক দিন পর রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'জগদীশচন্দ্র বসু' শিরোনামের একটি কবিতা। এর পর থেকে তাঁদের বন্ধুত্ব শুরু। রবীন্দ্রনাথ যেমন উৎসাহ দিয়ে বন্ধুর বিজ্ঞান গবেষণায় উজ্জীবিত রাখেন, জগদীশও তেমনি রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করে তোলেন।
ইউরোপে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য অনুবাদ করে তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুদের পড়ে শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা চিঠিতে জগদীশ বলেন, 'তোমার পুস্তকের জন্য আমি অনেক মতলব করিয়াছি। তোমাকে যশোম-িত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তর্জমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারে না। তবে কী করিয়া ঢ়ঁনষরংয করিতে হইবে, এখনও জানি না। চঁনষরংযবৎ-রা ফাঁকি দিতে চায়।' জগদীশ চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিম-লে উঠে আসুক; রবির আলোয় সারা পৃথিবী আলোকিত হোক। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের এক অপূর্ব সেতুবন্ধন হয়েছিল এ দুই মহান ব্যক্তির বন্ধুত্বের মাধ্যমে।
১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার অর্জনের মধ্য দিয়ে জগদীশের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা সফল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এ নোবেল বিজয়ে জগদীশের তাই আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না। এ অনুভূতিতে জগদীশ লেখেন, 'পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্য ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল। দেবতার এই করুণার জন্য কি করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব? চিরকাল শক্তিশালী হও, চিরকাল জয়যুক্ত হও। ধর্মর্ তোমার চিরসহায় হউন।'
রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়, তার সভাপতি ছিলেন স্বয়ং জগদীশচন্দ্র বসু।
১৯১৭ সালের ৩০ নভেম্বর নিজের ৫৯তম জন্মদিনে কলকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নিজ দেশে একটি বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন শুরু হয়।
জগদীশ তাঁর জীবদ্দশায় অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন।
১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ভারত সরকার তাঁকে সিআইই (ঈযধসঢ়রড়হংযরঢ় ড়ভ ঃযব ওহফরধহ ঊসঢ়রৎব) উপাধি, ১৯১২ সালে জগদীশ সিএসআই (ঈড়সঢ়ধহরড়হংযরঢ় ড়ভ ঃযব ংঃধৎ ড়ভ ওহফরধ) উপাধি, ১৯১৭ সালে নাইট উপাধিতে ভূষিত হন তিনি। ১৯২৬ সালে বেলজিয়ামের রাজা জগদীশচন্দ্র বসুকে রাজকীয় কমান্ডার অব দি অর্ডার অব লিওপোল্ড উপাধিতে ভূষিত করেন।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে।
এছাড়া ১৯২০ লন্ডন রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। পৃথিবীর যে কোনো বিজ্ঞানীর জন্যই এটি একটি বিরাট স্বীকৃতি। জগদীশচন্দ্র বসুই হলেন ভারতবর্ষের প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৯ সালে দশমবারের জন্য ইউরোপ যাত্রা করেন এবং ফিনল্যান্ডের বিজ্ঞান সমিতি কর্তৃক সংবর্ধিত হন।
১৯৩৭ সালের ২ নভেম্বর রায়বাহাদুর এএন মিত্রের আমন্ত্রণে সস্ত্রীক গিরিডি যাত্রা করেন। ২৩ নভেম্বর সকাল ৮টায় গিরিডিতে হঠাৎ বাথরুমে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। ২৪ নভেম্বর ভোর ৪টা ১২ মিনিটে গিরিডিতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মরদেহ নিয়ে আসা হয় বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে মরদেহ নিয়ে শেষ যাত্রা শুরু হয়; আর পার্ক সার্কাস ক্রিমেটরিয়ামে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
জগদীশের আজন্ম সাধনা ছিল সত্য অনুসন্ধান। জগদীশ জানতেন সত্যই জ্ঞান। জগদীশ মনে করতেন কবি, ঋষি, বিজ্ঞানী সবাই জ্ঞানের সাধক, সত্যের সাধক। কবি ও বিজ্ঞানীর সত্য অনুসন্ধিৎসার প্রসঙ্গে জগদীশ বলেছেন, 'বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না।'
জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানের পথেই সত্য অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। এ কারণেই তিনি 'বিশ্বাসের সত্য'কে 'বিজ্ঞানের সত্য' দিয়ে যাচাই করে এ দুয়ের ব্যবধান ঘোচাতে চেয়েছেন। বালক বয়সে জগদীশ চেয়েছিলেন উঁচু-নিচুর ব্যবধান ঘোচাতে। তরুণ বয়সে চেয়েছিলেন শাসক আর শোষিতের ব্যবধান ঘোচাতে। পরিণত বয়সে জগদীশের এ চেতনাই যেন পরিপক্ব হয়ে আরও উন্নত হয়ে ধরা দিয়েছিল তাঁর গবেষণায়। এ কারণেই তিনি ঘোচাতে চেয়েছেন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ব্যবধান, বিজ্ঞান-সাহিত্যের ব্যবধান, উদ্ভিদ-প্রাণীর ব্যবধান, এমনকি সপ্রাণ-অপ্রাণের ব্যবধানও। জগদীশের আজন্ম সাধনা ছিল এ ব্যবধান ঘোচানো। এ ব্যবধান ঘোচাতে গিয়ে জগদীশ সাফল্যের এমন এক গগনচুম্বী উচ্চতায় আরোহণ করেছেন, যেখানে খুব কম লোকের পক্ষেই যাওয়া সম্ভব। পৃথিবীর অসাধারণ সফল মানুষের মধ্যেও জগদীশ আলাদা। বাঙালির মধ্যে জগদীশ অনন্য, সবার চেয়ে এগিয়ে। এ কারণেই জগদীশ আজও প্রাসঙ্গিক, জগদীশ আজও গুরুত্বপূর্ণ।